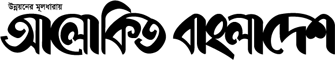সংস্কারের দোরগোড়ায় বাংলাদেশ : ঐকমত্যের আবরণে লুকানো অনিশ্চয়তা
এসএম রায়হান মিয়া
প্রকাশ : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐকমত্য শব্দটি একাধারে আশার প্রতীক, আবার ব্যর্থতার ছায়াও বয়ে আনে। প্রতিবারই যখন কোনো বড় রাজনৈতিক সংস্কারের দরজায় জাতি পৌঁছায়, তখনই ঐকমত্যের আহ্বান ওঠে- কখনও তা অর্জিত হয়, কখনও অধরা থেকে যায়। এবারের ‘জুলাই সনদ’ সেই দীর্ঘ ঐতিহ্যের সর্বশেষ সংযোজন- একটি দলিল, যা সংস্কার ও পুনর্গঠনের মহাপরিকল্পনা হিসেবে উন্মোচিত হলেও, তার ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চয়তার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।
দলীয় বিভাজন, রাষ্ট্রীয় অচলাবস্থা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক নিস্তেজতার পর যখন ছাত্রনেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থান এক নতুন জাগরণের সূত্রপাত ঘটায়, তখনই জন্ম নেয় এই সনদের ধারণা। উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট- রাষ্ট্রের কাঠামোগত পুনর্গঠন, ক্ষমতার ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া। কিন্তু সেই স্বপ্নের বীজ বপনের পরও অঙ্কুরোদ্গমের নিশ্চয়তা এখনও অনিশ্চিত। কারণ, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- বাংলাদেশে সংস্কারের ধারণা প্রায়ই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, অবিশ্বাস এবং অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির যজ্ঞে বিলীন হয়ে গেছে।
ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি গঠিত ‘ঐকমত্য কমিশন’ ছিল এই সনদের আত্মা। তাদের দায়িত্ব ছিল ছয়টি সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো একত্রিত করে একটি বাস্তবমুখী সনদে রূপ দেওয়া। সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনপ্রশাসন এবং স্থানীয় সরকার- এই ছয়টি ক্ষেত্রের সংস্কারকে কেন্দ্র করে ৮৪টি প্রস্তাবের ওপর ঐকমত্য অর্জন করা হয়, যা শেষ পর্যন্ত “জুলাই সনদ” নামে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।
এই সনদে এমন কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রস্তাব এসেছে, যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য পুনঃনির্ধারণ, নির্বাচনের নিরপেক্ষতা রক্ষায় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন, বিচারব্যবস্থার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সরকারে ক্ষমতা হস্তান্তর, এবং নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য সীমিত করা- এসবই একটি কাঠামোগত সংস্কারের ঘোষণা। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে, ঘোষণাপত্র ও বাস্তবতার মধ্যবর্তী ব্যবধানই বাংলাদেশে সংস্কারের সবচেয়ে বড় অন্তরায়।
জুলাই সনদের ঝুঁকিও সেখানেই। যদি এটি শুধু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির এক অলঙ্কার হয়ে থাকে, যদি এর সঙ্গে কোনো সময়নির্ধারিত রোডম্যাপ না থাকে, তবে এটি দ্রুতই পরিণত হবে সেই দীর্ঘ তালিকার অংশে- যেখানে পূর্ববর্তী সংস্কার কমিশনের সুপারিশ, পরামর্শ ও প্রতিশ্রুতিগুলো ধুলোমলিন ফাইলে নিস্তব্ধ পড়ে আছে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই প্রবণতার এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। ১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের আগে যে তিন জোটের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল- সেই ঐতিহাসিক দলিলেও গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সংস্কারের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ছিল। কিন্তু গণতন্ত্র ফিরে আসার পর ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নে দলগুলো নিজেদের সুবিধার গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সংস্কারের মহৎ অঙ্গীকার রয়ে যায় কাগজের পাতায়, আর বাস্তবে শুরু হয় নতুন এক দলীয় আধিপত্যের যুগ।
এরপর ১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গঠিত ২৯টি টাস্কফোর্স সংস্কারের ইতিহাসে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে সেসব টাস্কফোর্স ২৯টি খাতভিত্তিক নীতিনির্ধারণী প্রতিবেদন তৈরি করে, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, দুর্নীতির রোধ এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মতো বাস্তবভিত্তিক প্রস্তাব ছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর সেই সুপারিশগুলোও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে হারিয়ে যায়।
২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আকবর আলী খানের নেতৃত্বে “রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন (আরআরসি)” আবারো সেই হারানো সংস্কারের আলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। ১৫৩টি প্রস্তাবনা, যার মধ্যে অনেকগুলো প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে দিতে পারত, বাস্তবায়নের আগেই থমকে যায় রাজনৈতিক অনীহায়। আওয়ামী লীগ সরকারের অনিচ্ছা, আমলাতান্ত্রিক প্রতিরোধ এবং রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে আকবর আলী খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আজও সেই ১৩১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার প্রতীক হয়ে পড়ে আছে- একটি অপূর্ণ সংস্কারের কঙ্কালসার দলিল হিসেবে।
এই প্রেক্ষাপটে “জুলাই সনদ” নিঃসন্দেহে এক পুনর্জাগরণের আহ্বান। এটি কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এক ঐকমত্য নয়; বরং এটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নকশা নির্ধারণের এক সাহসী প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায়- এটি কি বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা তৈরি করতে পারবে?
সনদের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ সম্ভবত দুই কক্ষবিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাব। অনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে উচ্চকক্ষ নির্বাচিত হলে তা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রে বহুত্ববাদী প্রতিফলন ঘটাবে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এটি কতটা কার্যকর হবে, সেটিই বড় প্রশ্ন। দলীয় প্রধানদের সর্বময় নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজনৈতিক কাঠামোতে উচ্চকক্ষ কেবল আনুষ্ঠানিক বিরোধিতার একটি প্রতীক হয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি আবারও পুরোনো বিতর্ক উসকে দিয়েছে। একদিকে, এটি নির্বাচনের নিরপেক্ষতা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে জনগণের আস্থা পেতে পারে; অন্যদিকে, এটি ২০১১ সালের সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাতিল হওয়া একটি কাঠামোকে ফিরিয়ে আনার ঝুঁকি তৈরি করছে। প্রশ্ন উঠছে- বাংলাদেশ কি সত্যিই রাজনৈতিকভাবে পরিণত হয়েছে, যেখানে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে? যদি না হয়ে থাকে, তবে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার পুনরাগমন আসলে গণতন্ত্রের দুর্বলতাকেই স্বীকার করে নেওয়া হবে।
আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছরে সীমিত করা এবং একইসঙ্গে দলের প্রধান না থাকার প্রস্তাব- যা কার্যত বাংলাদেশে পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতির অবসানের পথে এক বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবও আপাতত কাগজে বন্দি। কারণ, বৃহৎ দলগুলো ইতোমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছে- তারা এই ধারায় সংশোধনী চাইবে। বাস্তবিক অর্থে, নেতৃত্বের নবায়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন বহু মুহূর্ত এসেছে, যখন জাতি নতুন সূচনার স্বপ্ন দেখেছে- কিন্তু তা অচিরেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। একবার ক্ষমতা অর্জনের পর দলগুলো সংস্কারের চেয়ে ক্ষমতার সংরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র তখন পুনর্গঠনের বদলে পুনর্ব্যবহারের যন্ত্রে পরিণত হয়। আজকের ‘জুলাই সনদ’ সেই বৃত্ত ভাঙার একটি সুযোগ এনে দিয়েছে।
তবে এই সুযোগকে কার্যকর করতে হলে প্রয়োজন তিনটি বিষয়- সময়সূচিবদ্ধ রোডম্যাপ, স্বাধীন বাস্তবায়ন কমিশন, এবং নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। সংস্কার যদি কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর হাতে থাকে, তবে তা অনিবার্যভাবেই তাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার হবে। সুতরাং নাগরিক পর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী সংগঠন ও সুশীল সমাজকে যুক্ত করা জরুরি।
তাছাড়া সংস্কারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। ইতিহাসে দেখা গেছে- বাংলাদেশে সংস্কার উদ্যোগগুলো সাধারণত সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। এক সরকারের নীতিকে পরবর্তী সরকার “বিরোধিতার রাজনীতি”র অংশ হিসেবে বাতিল করে দেয়। অথচ রাষ্ট্রের নীতি ও প্রশাসনিক কাঠামো দলীয় নয়; এটি জাতীয়। তাই জুলাই সনদের সফলতা নির্ভর করছে এই সত্যটি উপলব্ধি করার ওপর- সংস্কার কোনো একদলীয় কর্মসূচি নয়, এটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের যাত্রাপথ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কার হবে, নাকি সংস্কারের জন্য আবারও নতুন ঐকমত্য তৈরি করতে হবে? বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা গেছে, ঐকমত্য প্রায়ই রাজনৈতিক বাস্তবতার চাপে ভেঙে পড়ে। কারণ এখানে ঐকমত্যের উদ্দেশ্য অনেক সময় সংস্কার নয়, বরং ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস। অথচ প্রকৃত ঐকমত্য মানে হলো নীতিগত সম্মিলন- যেখানে লক্ষ্য থাকে রাষ্ট্রের কল্যাণ, কোনো দলের নয়।
যদি জুলাই সনদ সত্যিই সেই নীতিগত ঐকমত্যের প্রতিফলন হয়, তবে এটি এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারে। কিন্তু যদি এটি শুধু সাময়িক রাজনৈতিক আপসের ফল হয়, তবে এর পরিণতি হবে আগের মতোই- প্রতিশ্রুতির এক শূন্য দলিল, যার পাতায় থাকবে শুধুই শব্দ, বাস্তবে থাকবে নিস্তব্ধতা।
অতএব, এখন সময় এসেছে সনদের স্বাক্ষর থেকে বাস্তবায়নের পথে পদক্ষেপ নেওয়ার। সংস্কার কমিশনগুলোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি জাতীয় রোডম্যাপ তৈরি করে সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। সেই রোডম্যাপে থাকবে নির্দিষ্ট সময়সূচি, বাস্তবায়নযোগ্য ধাপ এবং নাগরিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা। শুধু তখনই জুলাই সনদ একটি “জীবন্ত দলিল” হিসেবে টিকে থাকবে- যে দলিল রাষ্ট্রের পুনর্জাগরণের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশ আজ এক ক্রান্তিকালে। অতীতের ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির মধ্যবর্তী এই সঙ্কটময় সময়টিই নির্ধারণ করবে- আমরা কি আবারও সংস্কারের স্বপ্নকে দলীয় কোলাহলে হারাব, নাকি সত্যিই একটি নতুন রাষ্ট্রীয় দর্শনের পথে যাত্রা শুরু করব। ঐকমত্যের জন্য সংস্কার নয়, বরং সংস্কারের প্রয়োজনে ঐকমত্য- এই ধারণাটিই এখন জাতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ।
যদি আমরা সেই সুযোগকে গ্রহণ করতে পারি, তবে জুলাই সনদ শুধু একটি রাজনৈতিক চুক্তি থাকবে না; এটি হয়ে উঠবে বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক যাত্রার নীলনকশা- যেখানে রাষ্ট্র, নাগরিক ও গণতন্ত্র এক অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে যুক্ত হবে। কিন্তু যদি আমরা ব্যর্থ হই, তবে এটি হবে আরেকটি হারানো অধ্যায়ের সূচনা- যেখানে আবারও ইতিহাস বলবে, আমরা ঐকমত্য অর্জন করেছিলাম; কিন্তু সংস্কার করতে পারিনি।
এসএম রায়হান মিয়া
সিনিয়র শিক্ষক ও কলাম লেখক গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা