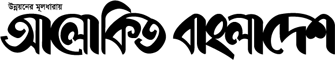পরিবেশ রক্ষায় রাজনীতি ও নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা
আল শাহারিয়া
প্রকাশ : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ বিপর্যয় কোনো কাল্পনিক বা দূরবর্তী কোনো সমস্যা নয়। এটি এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এক রূঢ় বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তীব্র দাবদাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে এবং অসময়ে বন্যার হানা ফসলি জমি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় জনপদকে গ্রাস করছে। এসব ঘটনাকে শুধু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে সতর্ক করে আসছেন যে এই বিপর্যয়ের মূল কারণ মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড। তবে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা প্লাস্টিক বর্জন বা গাছ লাগানোর মাধ্যমে যতটুকু ভূমিকা রাখতে পারি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রভাব ফেলে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত। পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি এখন আর শুধু সামাজিক সচেতনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং এটি পুরোপুরি রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।
একটি দেশের পরিবেশ কতটা সুরক্ষিত থাকবে তা নির্ভর করে সেই দেশের নীতিনির্ধারকদের দূরদর্শিতার ওপর। রাজনীতি ও পরিবেশকে অনেকে আলাদা করে দেখতে চান। কিন্তু আদতে এ দুটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও শিল্পায়ন নীতি সরাসরি প্রকৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। যখন কোনো সরকার বা নীতিনির্ধারক মহল পরিবেশকে উপেক্ষা করে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে নজর দেন তখন দীর্ঘমেয়াদে তা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হয়। তথাকথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে বন উজাড় করা বা নদী ভরাট করার প্রবণতা আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি। এসব প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা থাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে। তাই পরিবেশ ধ্বংসের দায়ভারও তাদের ওপরই বর্তায়।
আমাদের নীতিনির্ধারণী মহলে প্রায়ই একটি ভুল ধারণা কাজ করে। তারা মনে করেন পরিবেশ রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পরবিরোধী। তাদের যুক্তি হলো কঠোর পরিবেশ আইন প্রয়োগ করলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে এবং কর্মসংস্থান কমবে। অথচ উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা এর উল্টো চিত্র দেখতে পাই। টেকসই উন্নয়ন বা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টের মূল কথাই হলো পরিবেশকে অক্ষত রেখে অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের ধীরগতি লক্ষ্যণীয়। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বা দূষণকারী শিল্পের অনুমোদন দেওয়ার আগে পরিবেশগত প্রভাব যাচাই অনেক সময় লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। এখানে রাজনীতির একটি বড় প্রভাব থাকে। প্রভাবশালী মহলের চাপে অনেক সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।
শহরাঞ্চলের পরিবেশ বিপর্যয়ের দিকে তাকালে আমরা নীতিনির্ধারণী দুর্বলতার চিত্রটি আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। অপরিকল্পিত নগরায়ন আমাদের শহরগুলোকে একেকটি হিট আইল্যান্ডে পরিণত করেছে। জলাশয় ভরাট করে আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলার সময় শহরের তাপমাত্রা বা ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের কথা ভাবা হয়নি। এসব প্রকল্প রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় বা নীতিনির্ধারকদের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণেই বাস্তবায়িত হয়েছে। শহরের বাতাস আজ বিষাক্ত এবং এর প্রধান কারণ ফিটনেসবিহীন যানবাহন ও কলকারখানার কালো ধোঁয়া। এসব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন আছে; কিন্তু আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এই অরাজকতা বন্ধ করা কঠিন কিছু ছিল না। গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আধুনিক না করে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার উৎসাহিত করার নীতিও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। একটি জনবান্ধব ও পরিবেশবান্ধব নগরী গড়তে হলে রাজনৈতিক দর্শন ও পরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।
নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীর মৃত্যু এখন এক সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নদীর তীর দখল করে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ বা নদীতে শিল্পবর্জ্য ফেলার ঘটনা অহরহ ঘটছে। দখলদাররা প্রায়ই স্থানীয় রাজনীতি বা ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। নীতিনির্ধারকরা নদী রক্ষায় কমিশন গঠন করেন ও বড় বড় প্রকল্পের ঘোষণা দেন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত নড়বড়ে। নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করার পরেও এর ওপর অত্যাচার কমেনি। এর কারণ হলো নদী রক্ষার চেয়ে দখলদারদের স্বার্থরক্ষা অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি ইশতেহারে পরিবেশ রক্ষার প্রতিশ্রুতি থাকে ঠিকই কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন খুব একটা দেখা যায় না। যতদিন পর্যন্ত নদী ও জলাশয় রক্ষাকে রাজনৈতিক এজেন্ডার শীর্ষে না রাখা হবে, ততদিন এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না।
জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও রাজনীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বড় বড় বুলি আওড়ানো হয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলো তাদের শিল্পস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে বলে কার্বন নিঃসরণ কমাতে গড়িমসি করে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোও উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ভয়ে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে পুরোপুরি ঝুঁকতে পারছে না। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। আন্তর্জাতিক দরকষাকষিতে আমাদের নীতিনির্ধারকদের আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু ক্ষতিপূরণ দাবি করাই যথেষ্ট নয়। দেশের অভ্যন্তরেও পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে হবে যে আমরা পরিবেশ রক্ষায় আন্তরিক। জলবায়ু তহবিল থেকে পাওয়া অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করাও নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব। দুর্নীতির কারণে অনেক সময় এই তহবিলের সুফল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছায় না যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।
পরিবেশ আইন ও বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা আরেকটি বড় বাধা। পরিবেশ দূষণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা হলে তা বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। অনেক সময় প্রমাণের অভাবে বা রাজনৈতিক প্রভাবে অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। পরিবেশ আদালতগুলোকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করা প্রয়োজন। নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে যে পরিবেশ অপরাধ অন্য সাধারণ অপরাধের চেয়ে কম গুরুতর নয়। কারণ এটি শুধু একজন ব্যক্তিকে নয় বরং পুরো সমাজ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
বনভূমি রক্ষা ও বনায়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। সামাজিক বনায়নের নামে অনেক সময় প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে বিদেশি দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগানো হয়। এটি জীববৈচিত্র্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে আমাদের রক্ষা করে আসছে। অথচ বিভিন্ন সময় সুন্দরবনের আশপাশে ভারী শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নীতিনির্ধারকদের মনে রাখা উচিত যে মুনাফার লোভে প্রাকৃতিক সুরক্ষা দেওয়াল ধ্বংস করলে তার মাশুল দিতে হবে বহু বছর ধরে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন তবে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না। তরুণ প্রজন্ম এখন পরিবেশ নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। তারা চায় তাদের নেতারা পরিবেশ রক্ষায় কঠোর হোক। গ্রিন পলিটিক্স এখন সময়ের দাবি। এর অর্থ হলো প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশকে কেন্দ্রে রাখা। বাজেট প্রণয়নের সময় পরিবেশ খাতে বরাদ্দ বাড়ানো এবং দূষণকারী শিল্পের ওপর উচ্চ হারে কার্বন ট্যাক্স আরোপ করা প্রয়োজন। প্লাস্টিক দূষণ রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বিকল্প পণ্যের বাজার তৈরিতে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে।
পরিবেশ রক্ষায় জনগণের সচেতনতা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তা ছাড়া কেবল ব্যক্তিগত সচেতনতা দিয়ে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। একজন নাগরিক হিসেবে আমরা রাস্তায় ময়লা ফেলা বন্ধ করতে পারি। কিন্তু কলকারখানার বর্জ্য নদীতে ফেলা বন্ধ করার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই। সেটি করার জন্য রাষ্ট্র ও নীতিনির্ধারকদের কঠোর হতে হবে। পরিবেশ রক্ষার লড়াইটি এখন আর শুধু পরিবেশবাদীদের লড়াই নয়। এটি আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে যে প্রকৃতি ধ্বংস করে কোনো উন্নয়নই টেকসই হয় না। প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে জানে এবং সেই প্রতিশোধ অত্যন্ত নির্মম হয়।
উপসংহারে বলা যায় যে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে রাজনীতি ও নীতিনির্ধারকদের ভূমিকাই মুখ্য। তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত লক্ষ কোটি মানুষের জীবন ও প্রকৃতির ভাগ্য নির্ধারণ করে। তাই তাদের আরও বেশি দায়িত্বশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক লাভের আশায় দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত ক্ষতি মেনে নেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে পরিবেশ সুরক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত করতে হবে। জনগণ চায় তাদের নেতারা পরিবেশের বন্ধু হোক। সুস্থ পরিবেশেই শুধু একটি সুস্থ জাতি ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে। তাই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই নীতিনির্ধারকদের ঘুম ভাঙাতে হবে এবং কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
আল শাহারিয়া
শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর