 প্রিন্ট সংস্করণ
প্রিন্ট সংস্করণ ০০:০০, ১১ জানুয়ারি, ২০২১
০০:০০, ১১ জানুয়ারি, ২০২১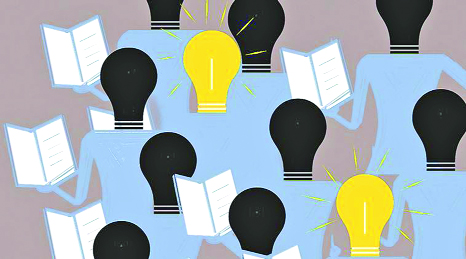
শুরুতে ছোট্ট এবং প্রচলিত একটি গল্পের অবতারণা করতে বাধ্য হচ্ছি। গল্পটা এরকম : প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন পরিদর্শক এলেন আগে থেকে কোনো রকম জানান না দিয়ে। ছাত্র-শিক্ষক সবাই শতর্ক অবস্থানে। পরিদর্শক প্রধান শিক্ষককে নিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রবেশ করলেন। ক্লাস ক্যাপটেন যথাযথ সম্মানজ্ঞাপন-পূর্বক স্বাগত জানালেন। ক্লাসশুদ্ধ দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করল। সম্মানজ্ঞাপন সূচক আনুষ্ঠানিকতা শেষে ছাত্রছাত্রীরা বসে পড়ার পর একজন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রুটিন অনুসারে এখন কোনো বিষয়ের ক্লাস হওয়ার কথা? জবাবে বলল বাংলা। পড়া (পাঠ) শিখেছ? ‘না স্যার, আমার ‘ছুখে’ ব্যথা।’ ‘আরেকজন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি শিখেছ? ‘না স্যার, আমার বই ‘ছুরে’ লই গেছে।’ এরপর আরেক ছাত্র বলে, ‘ভুইলা’ গেছিলাম। আরেক ছাত্র বলে ‘আগে আগে হুইয়া’ পড়ছিলাম। পরিদর্শক খানিকটা বিরক্ত হয়ে প্রধান শিক্ষকের উদ্দেশে বললেন, ছাত্ররা এসব কি আবোল-তাবোল বলছে? পরিদর্শকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রধান শিক্ষক বললেন, পড়া শিখে নাই ‘হেইটা’ এদের ‘দুষ’; কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রীরা মিছা কথা কয় না।
উল্লিখিত গল্পটা নিছক গল্প নয়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বা সমাজের বাস্তবতা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত থেকে বিদ্যালয়ের পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণরত অবস্থায়ও কি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা চোখকে ‘ছুখ’, চোরকে ‘ছুর’, দোষকে ‘দুষ’, এটাকে ‘হেইটা’ শুয়ে পড়াকে ‘হুইয়া পড়া’ এসবই শিখবে? গলদটা কোথায়? আমাদের শিক্ষাধারার বা ব্যবস্থাপনার? এসব আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। ভাষার শুদ্ধরূপ চর্চা করতে হবে। শিখতে হবে। পুরো ভাষাটাকে অর্জন করতে হবে। ভাষার শুদ্ধরূপ অর্জন করার, চর্চা করার সর্বোত্তম স্থান শ্রেণিকক্ষ আর শিক্ষক সমাজ এই সর্বোত্তম স্থানের রক্ষাকবচ। যাদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম হয়, শিক্ষার বীজ প্রোথিত হয়, ভবিষ্যৎ শিক্ষার গতিপথ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষা অর্জনে সঙ্গে শিক্ষকের প্রভাবও শিক্ষার্থীরা অর্জন করে এবং সেই অর্জনকে সঙ্গে করেই শিক্ষার্থীরা অগ্রসর হয়। এ তো গেল ভাষার কথা, শব্দ উচ্চারণের কথা। মানুষের জীবনচক্রে শিক্ষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে আর এ ভূমিকার একটি মজবুত স্তম্ভ প্রাথমিক শিক্ষা। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার। এই উচ্চারণ প্রক্রিয়া ছাড়াও সর্বজনীন শিক্ষার আরও বিভিন্ন দিক আছে, এসব অর্জন করতে হবে। আমাদের শিক্ষাধারাকে, শিক্ষাব্যবস্থাপনাকে সর্বোপরি শিক্ষক প্রশিক্ষণকে একটা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। শিক্ষক সমাজ আলোর দিশারি। কোমলমতি প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকের প্রভাব অপরিসীম। তাই সর্বাগ্রে আমাদের মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করতে হবে, মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারের জন্য।
এছাড়া শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর যুগে যুগে এটাই প্রমাণিত সত্য। কজেই শিক্ষার ধারাকে গতিশীল, যুগোপযোগী এবং কার্যকর করে গড়ে তুলতে, মানসম্মত শিক্ষাধারা বজায় রাখতে শিখন, শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের কার্যকর প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। একটি কার্যকর শিক্ষাধারার শিখন, শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ এই তিন পর্বের সঙ্গেই শিক্ষকের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
শিক্ষাধারা কি এবং কেন?
শিক্ষাধারা শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাচর্চার একটা পদ্ধতিগত ধারা। বিষয়টা সর্বজনীন। তাই শিক্ষাধারায় সর্বজনের এবং সর্ব বিষয়ের সম্পৃক্তি। শিক্ষার নানা ধরনের গতিপ্রকৃতিকে একত্রে শিক্ষাধারা বলে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের শিক্ষা লাভ শুরু হয় মায়ের ভ্রুণ থেকে। তবে জন্মের পর তার বোধশক্তির স্ফূরণকাল থেকে শিক্ষার প্রকৃত প্রস্তুতি দেখা যায়। চারপাশের পরিবেশ এবং তারই বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে শিশু শিখতে থাকে, ধীরে ধীরে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে। তারপরও নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ। এ ধরনের শিক্ষার তিনটি প্রধান ধারা হলো : আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সাধারণত বৃহত্তর শিক্ষাধারা, সুপরিকল্পিত, অনমনীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও যৌক্তিকভাবে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত প্রতিষ্ঠাননির্ভর শিক্ষা-কার্যক্রমের নাম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যত শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান ও শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং এই জ্ঞান শিখন ও অভিজ্ঞতানির্ভর আচরণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা স্তরভিত্তিক, বয়ঃক্রমিক, উদ্দেশ্যমূলক, দীর্ঘমেয়াদি, পূর্ণকালীন সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোভিত্তিক। সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুসারী, নির্দিষ্ট সময়সীমার শেষ পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ বিতরণ এবং আইন, বিধি, রীতি, প্রথা ও নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি অনমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশে সমাজের আইন-বিধি সংস্কার প্রথা ভেদে কিছু হেরফের হলেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য একই রকম।
আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট নিয়মের প্রতি আনুগত্য। এই ধারায় নির্দিষ্ট স্কুল ভবনে, বিধিবদ্ধ উপকরণের দ্বারা প্রথাগত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় ও বাংলাদেশে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন : প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, ইত্যাদির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীর চাহিদা, বাস্তবতা, আকাক্সক্ষা ইত্যাদির তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা-রক্ষাই বেশি গুরুত্ব পায়। বয়সভাগ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত।
অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা-নিয়মকানুনের নিগড়ে আবদ্ধ নয়, এমন শিক্ষাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ শিক্ষাকে বিধিবহির্ভূত শিক্ষাও বলা হয়। এ শিক্ষণ ও শিখন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবার, পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে যা কিছু শেখে তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এ শিক্ষার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ঠিক উল্টোটাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। এটি শিক্ষার প্রাচীনতম ধারা। মানুষের জীবনে শিক্ষার সূত্রপাত হয় অনানুষ্ঠানিক ধারায় এবং এ প্রক্রিয়া আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে একটি অনিঃশেষ প্রক্রিয়া। প্রাচীন সমাজে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই ছিল শিক্ষা লাভের একমাত্র উপায় এবং এ শিক্ষা ছিল সর্বজনীন। এ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় মানুষ শোনে, দেখে, অনুকরণ করে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে শিখে থাকে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিধিবদ্ধতার বাইরে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে শিক্ষাধারা গড়ে উঠেছে, তাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। নির্দিষ্ট বয়সে যারা বিভিন্ন কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি বা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্যই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার উদ্ভব। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মকানুনের কড়াকড়ি কম। শিক্ষাক্রম তুলনামূলকভাবে আকর্ষণীয় ও জীবনঘনিষ্ঠ। উপানুষ্ঠনিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে সৃষ্ট।
তবে এ শিক্ষায় যেমন রয়েছে খানিকটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ছোঁয়া, আবার যেমন রয়েছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার নিয়মকানুনের কিছুটা কড়াকড়ি। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মিলিত-ধারাই হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। মূলত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকাশ ঘটে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে গড়ে ওঠা একটি উদ্দেশ্যমূলক, পরিকল্পিত ও সুসজ্জিত শিক্ষাব্যবস্থা। এই বিকল্প শিক্ষাধারার উদ্দেশ্য, সময়, শিক্ষাক্রম, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে নমনীয়, সময় ও স্থানের দিক থেকে অবাধ, বিশেষ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা চাহিদা পরিপূরণে সচেষ্ট এবং সর্বোপরি মৌলিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে নানা শিখন পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তিকরণে সফল। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকা মোটেও মুখ্য নয়। এ ধারায় শেখার বিষয়টি নির্ভর করে শিক্ষার্থীর ওপর। এটি তার ব্যক্তিত্ব। জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পাশাপাশি বিশ্লেষণী ক্ষমতাও ভালোভাবে কাজ করতে দক্ষতা বাড়ায়।
ঐতিহাসিকভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করলেও ধীরে ধীরে এ শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সহজ শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে। অনেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোনো দেশেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমান্তরাল শিক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারাটি অবাধ ও নমনীয় হলেও এখানেও রয়েছে কিছু নিয়মনীতি, যেগুলো স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এ শিক্ষাধারাটি এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে সমন্বায়িত ও সম্প্রসারিত হয়নি। নিরন্তর সমন্বয়ের কাজ চলছে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে চালু হলেও নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত তা সুস্পষ্ট শিক্ষাধারার রূপ নেয়নি। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দাপ্তরিক প্রামাণক হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবহার দেখা যায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮)। তখন একে বাংলায় ‘অনানুষ্ঠানিক’ শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হত। পরবর্তী সময়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলো ‘গণশিক্ষা’ ও ‘অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা’ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঘড়হ ঋড়ৎসধষ ঊফঁপধঃরড়হ-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা’ প্রথম ব্যবহার করেন ড. আবু হামিদ লতিফ ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তার বই ‘উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষায়।
শিক্ষাধারা একটা বিস্তৃত বিষয়। শিক্ষার যে কোনো কর্মসূচি শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক এতসব ধারা থাকার পরও আমাদের শিক্ষাধারার অতিপ্রচলিত কিছু গলদ দূর হচ্ছে না কেন? শিক্ষণ, শিখন এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী বা গ্রহণকারী অথবা চর্চাকারীর অসাবধনাতাই কি এ জন্য দায়ী? অথবা কর্তৃপক্ষের অসাবধানতা? অর্থাৎ শিক্ষাধারার যা কার্যকারিতা হওয়া দরকার তা কার্যকর হচ্ছে না। এককথায় বর্ণিত শিক্ষাধারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না, যা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো বিষয়। প্রধানত ভুল শিক্ষাই এর জন্য দায়ী। আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে, প্রতিবেশে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে শ্রেণিকক্ষে বসে বিদ্যাচর্চা চলে সেখানে কেন ভুল শিক্ষার চর্চা ঘটে? এর কারণ কি শিক্ষকের, শিখনের, প্রশিক্ষণের, শিক্ষণের, না পুরো শিক্ষাপদ্ধতির? যে পদ্ধতিকে যুগ যুগ ধরে ধারণ করে এসেছি। আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টা পদ্ধতির। সঠিক পদ্ধতির প্রয়োগ গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। তাছাড়া মানুষের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা অপরিসীম। কাজেই সমাজে বিদ্যমান শিক্ষাধারা নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ ভুল শিক্ষা যেন শিক্ষার কোনো ধারা না হতে পারে। ভুলকে ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়ার বা কম গুরুত্ব দেওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ সামান্য একটা ভুলও সর্বনাশ ঘটাতে পারে। কাজেই সাবধানতা আমাদেরকেই অবলম্বন করতে হবে, অন্তত শিক্ষার্থীরা যেন কোনো অবস্থাতেই ভুলের কবলে না পড়ে শিক্ষাজীবনে। কাছের ভুল বা দূরের ভুল যে কোনো ভুলই অঘটন ঘটাতে পারে।
আমাদের দেখতে হবে ভুল শিক্ষার উৎপত্তি কোথায়? শিক্ষার্থীরা কেন ভুল করে? মোটা দাগে শিক্ষা অর্জনের অন্তত দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি সঠিক, আরেকটি ভুল। সঠিকধারা যতœসহকারে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অর্জন করতে হয়। অন্যটি ভুল, যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে চরম ভোগান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত ভুল বানান, ভুল বাক্য ও ভুল ছাপার কারণে যে ভুল বিষয় শিখছে, শ্রেণিকক্ষে ভুল শিক্ষাচর্চা করছে তাই ভুল শিক্ষা। যেমন বানানের ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষার্থী ‘ভুল’ শব্দটি লিখতে গিয়ে ‘ভূল’ লিখে; ‘অঙ্ক’ (অঙকো) শব্দটি লিখতে গিয়ে ‘অংক’ লিখে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছাপার ভুলের কারণেও এসব ভুল হয়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত তথ্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক যথাযথভাবে উপস্থান ও বিশ্লেষণ না হওয়ার কারণেও শিক্ষার্থীরা ভুল শেখে।
এছাড়া বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ফলে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও ইচ্ছে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের নামে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো তথ্য সন্নিবেশিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা ভুল শেখে। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা বা প্রচলিত ব্যবহারিক শিক্ষাধারার ভূমিকা বা গলদ এখানেই। সার্বিকভাবে সর্বজনীন শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যথাযথ উদ্যোগের ফলে এই গলদ কর্তন করা অথবা খানিকটা খর্ব করা অসম্ভব নয়। গলদযুক্ত শিক্ষা সুশিক্ষার অন্তরায়। দীর্ঘদিনের অযতœ এবং অবহেলায় শিক্ষাধারার পরতে পরতে মিশে থাকা গলদ নির্মূল অথবা নিদেনপক্ষে খানিকটা খর্ব করাই শিক্ষাধারার মৌলিক ভূমিকা বিকাশে সহায়ক। শিক্ষা হোক শিক্ষণীয়, আগামী প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। শিক্ষাধারার উপকরণ শিখন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ হোক গলদমুক্ত এবং রচিত হোক শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সঠিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এমনটাই আমাদের প্রত্যাশা। এক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো শিশুর মন ও পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধ তৈরি করা, উদ্দীপনা জাগিয়ে দেওয়া। আর শিক্ষক যদি শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে বা নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে যতবান না হন, তাহলে শুরুতে উল্লেখিত সেই গল্পের মতো ‘দুষ’, ‘ছুখ’, ‘ছুর’ এসব শব্দগোত্র দাপিয়ে বেড়াবে যেটা মোটেও প্রত্যাশিত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষাদান পদ্ধতির ‘গলদ’ই শিখনের গলদ হয়ে বাস্তবজীবনে বা শিখন প্রয়োগ ক্ষেত্রে আমাদের কলুষিত করবে।