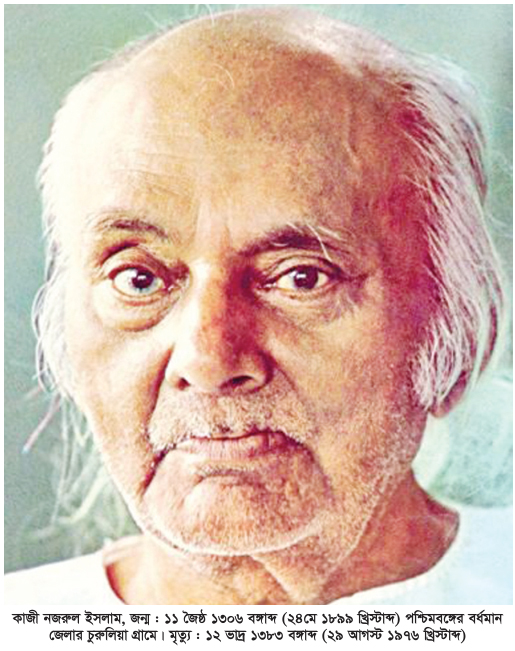
কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি যেদিন কবির মস্তিষ্কের নিবাস ছেড়ে পৃথিবীর পথে পা বাড়াল, সেদিন ছিল ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের শীতকাতর রাত, পৌষের হাড় হিম করা সময়। ঊনিশশ’ একুশের শেষ মাসে কাগজে-পেন্সিলে যে কবিতাটি তরুণ কবির হাত ধরে জন্ম নেয়, তার হদিস অন্য মানুষেরা পেতে সময় নিল আরও কয়েকটা দিন। দিন গড়াতে গড়াতে একুশ গিয়ে বাইশ সালের জানুয়ারি এসে পড়ে। এ মাসের ছয় তারিখেই ‘বিজলী’ পত্রিকা পায় তার মাতৃত্বের অধিকার। ‘বিজলী’র পরপর দুটো সংস্করণ করতে হয়েছিল ‘বিদ্রোহী’ কবিতার কল্যাণে ও এ দুই সংস্করণেই মোট ঊনত্রিশ হাজার কপি ছাপতে হয়েছিল। অথচ কবিতাটি প্রথমে ‘মোসলেম ভারত’ পেলেও ছাপতে দেরি হওয়ার কারণে ‘সাপ্তাহিক বিজলী’ই তার প্রথম প্রকাশ্য মাতৃত্বের স্বাদ পায়। এর পর ক্রমে ক্রমে একযোগে মাসিক প্রবাসী, মাসিক সাধনা ও দৈনিক বসুমতী ও ধূমকেতুতে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় এত বিরোধিতা কোনো কবিতাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে বলে জানা নেই। নজরুলের ‘বিদ্রোহী’র প্রতি আঘাত হানেন সাহিত্য সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, যিনি তার লেখা গদ্য ‘আমি’কে মনে করেন ‘বিদ্রোহী’র সূতিকাগার। কবি গোলাম মোস্তফা ‘বিদ্রোহী’কে প্যারোডি করে ব্যঙ্গ করেন ‘নিয়ন্ত্রিত’ কবিতার মাধ্যমে। স্বল্পখ্যাত কবি গোলাম হোসেন ‘বিদ্রোহী এক ইবলিস’ নামের কবিতার আঘাতে কবিকে আহত করার অপচেষ্টা করেন। কবি ও সম্পাদক (‘ইসলাম দর্শন’ পত্রিকা) আবদুল হাকিম ‘বিদ্রোহ দমন’ নাম দিয়ে একটি কবিতা লিখে নজরুলকে অপমানিত করার চেষ্টা করেন সর্বাত্মক।
ইসলাম দর্শন পত্রিকার সম্পাদক আবদুল হাকিম রীতিমতো অশালীন ভাষায় নজরুলকে আক্রমণ করেন ‘বিদ্রোহ দমন’ শিরোনামের একটি কবিতা লিখে। মোহাম্মদ গোলাম হোসেন নামের একজন কবি একটি কবিতা লেখেন, যার শিরোনাম ছিল ‘বিদ্রোহী এক ইবলিস’। নজরুলের কাছের লোকদের মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফা ‘বিদ্রোহী’ কবিতার ব্যঙ্গাত্মক প্যারোডি রচনা করেন ‘নিয়ন্ত্রিত’ শিরোনামে। ‘শনিবারের চিঠি’র সজনী কান্ত দাস ‘আমি সাপ, ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই’ বলে যে আক্রমণ করেন, তাতে অন্য কেউ হলে কুপোকাত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাইশ বছরের টগবগে যোদ্ধা তরুণ সেসবকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান তরতর করে রকেট গতিতে।
ছয় মাত্রার মুক্তক মাত্রাবৃত্তের একশ’ তেতাল্লিশ পঙ্ক্তির কবিতাটি নিয়ে যে মিথ প্রচলিত আছে তাতে বলা যায়, কবিতাটি রচিত হয়নি বরং ভর করেছিল কবি কাজী নজরুলের মস্তিষ্কে। নাজেল হওয়া কবিতাটি যাতে গড় গড় করে তিনি লিখতে পারেন, সে কারণেই হয়তো কলমের পরিবর্তে কবি পেন্সিল ব্যবহারের যৌক্তিকতা অনুধাবন করেছিলেন। তখনকার কলমকে বারবার কালির দোয়াতে ডোবাতে গেলে মাথায় ভর করা কবিতাটি খেই হারাতে পারেÑ এ ভয়েই পেন্সিল এখানে লিপিকারের ভূমিকা পালন করে। এ মিথটি অনেকাংশেই মুনি ব্যাসদেব ও সিদ্ধিদাতা গণেশের ‘মহাভারত’ রচনার মিথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষত ভোরে রক্তজবা লাল দু’চোখ নিয়ে কবি যখন তার প্রথম শ্রোতা বন্ধু মুজফ্ফর আহমদকে কবিতাটি শ্রবণ করান তখন এটা মনেই হতে পারে, দৈববাণীর মানবশ্রুতি ঘটেছে। অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোক হতে আহৃত শব্দশিল্প প্রথম মনুষ্যগোচর হলো মুজফ্ফর আহমদের মাধ্যমেই।
রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে ‘বিদ্রোহী’ বিনির্মিত হলেও এতে প্রেম, অসাম্প্রদায়িকতা, প্রকৃতি ও পুরাণ, সমাজ বাস্তবতাÑ সবই স্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। দেবী ইন্দ্রানী হতে শুরু করে প্রেমনন্দিনী ষোড়শী তন্বী কিংবা বিধবা পল্লিবালাকে কবি যেমন বিদ্রোহীর অঙ্গে অঙ্গে স্থান দিয়েছেন, তেমনি স্থান দিয়েছেন জগতের তাবৎ শোষিতকে। যে বিদ্রোহীর ছবি কবি পঙ্ক্তিতে পঙ্ক্তিতে এঁকেছেন, সে বিদ্রোহী কোনো একক সত্তা নয়, বরং এই বিদ্রোহী এক সামষ্টিক সত্তা, যার এক একটি ব্যক্তিক রূপ সামগ্রিক বিদ্রোহীকে ফুটিয়ে তোলে। শোষকের বিরোধী হয়ে শোষিতের পক্ষধারণকারী বিদ্রোহীরূপে সর্বকালের সেরা বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন এ কবিতায় পরবর্তী সময়ে পঞ্চাশ বছর পরে এসে রূপায়িত হন, তেমনি রুশ বিপ্লবের লেলিন কিংবা যুগাবতার ও ‘যত পথ তত মত’-এর স্বপ্নদ্রষ্টা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও ব্যবহৃত রূপকের মাধ্যমে বিদ্রোহীর ব্যক্তিক রূপ হিসেবে প্রকটিত হয়ে ওঠেন।
বিদ্রোহী কবিতাটি যতটা না অন্যের মাঝে ভীতি সঞ্চারের বজ্রনিনাদ, তার চেয়ে বরং অধিকভাবেই নিজেকে চিনিয়ে তোলার দৃপ্ত প্রয়াস। বিদ্রোহী কবিতার ভাষা কোমল না হলেও এর উদ্দেশ্য কোমল। উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল স্তব্ধ করতে অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভেঙে ফেলার মানবিক প্রয়াসই বিদ্রোহীর মূল লক্ষ্য। তাই কবিতায় যেমন মাতা মেরি-তনয়, ক্রুশবিদ্ধ যিশু যেমন এসে প্রেম বিলানোর কথা বলে যান, তেমনি গৈরিক বসনধারী রাজবেশ ছেড়ে আসা সিদ্ধার্থ গৌতমও কবিতার ছত্রে ছত্রে মৈত্রী ও করুণার ফল্গুধারা ছোটান। বিদ্রোহী পিনাক-পাণির রুদ্র প্রলয়ের ভয় যেমন জাগিয়ে শান্তির কথা বলে, তেমনি ইস্রাফিলের শিঙ্গা ফুঁকিয়ে বা অর্ফিয়ুসের বাঁশি বাজিয়েও আধ্যাত্মিকতা যাপন করেন। বিদ্রোহীর পরতে পরতে মানবিকতা ও আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্বোধন ঘটেছে বলেই আজ শতবর্ষ পেরিয়েও ‘বিদ্রোহী’র আদর ও জদর এতটুকু ম্লান হয়নি। শতবর্ষের প্রবীণ হয়েও ‘বিদ্রোহী’ আজও সমকালীন, আজও সমান প্রাসঙ্গিক তার রচনাকালের মতোই।